ফেক নিউজ চেনার ৯টি উপায়
বর্তমান ডিজিটাল যুগে, তথ্য প্রযুক্তির প্রসার সমাজে অসাধারন পরিবর্তন এনে দিয়েছে। তবে, তথ্য প্রযুক্তির এই বিপ্লবের সাথে সাথে একটি গভীর সমস্যাও দেখা দিয়েছে; সেটি হলো ফেক নিউজ বা ভুয়া খবরের প্রসার। ফেক নিউজ খুব তাড়াতাড়ি বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পরে, যা জনমতকে প্রভাবিত করে, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বদলে দেয়, এমনকি এটি ব্যাক্তিগত সম্পর্কেরও ক্ষতি সাধন করতে পারে।
এই সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য, পাঠকদের সত্য ও মিথ্যা সংবাদের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য সমালোচনামূলক দক্ষতা অর্জন করা জরুরি। এই আর্টিকেলে ফেক নিউজ চেনার নয়টি কার্যকর উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যার ফলে পাঠকরা আজকালকার জটিল মিডিয়া পরিবেশে সঠিক তথ্য ও সংবাদ বেছে নিতে সক্ষম হতে পারবে।
সূচিপত্রঃ ফেক নিউজ চেনার ৯টি উপায়
- সংবাদের উৎস মূল্যায়ন করুন
- হেডলাইন চেক করুন
- লেখকের সম্পর্কে জানুন
- সংবাদ প্রকাশের তারিখ দেখুন
- প্রতিবেদনের বিষয় চেক করুন
- প্রতিবেদনের তথ্যগুলোকে ক্রস রেফারেন্স করুন
- প্রতিবেদনের টোন এবং উদ্দেশ্য নির্নয় করুন
- সংবাদ প্রতিবেদনের সাথে পাঠকদের অংশগ্রহন খেয়াল করুন
- তথ্যগুলোর সত্যতা যাচাইয়ে বিশেষ সাহায্য নিন
- শেষ কথা
সংবাদের উৎস মূল্যায়ন করুন
একটি সংবাদ প্রতিবেদন কতটা বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে তা প্রায়ই তার উৎসের উপর নির্ভর
করে। নামকরা সংবাদ মাধ্যমগুলো সাংবাদিকতার মানদন্ড মেনে চলতে চেষ্টা করে, যার
মধ্যে রয়েছে তথ্য যাচাই ও নৈতিক রিপোর্টিং করা। সংবাদের বিশ্বাসযোগ্যতা যাচাই
করতে হলেঃ
প্রকাশকের ইতিহাস যাচাই করে দেখুনঃ আপনি
অনলাইনে যে খবর পড়ছেন তা নির্ভরযোগ্য কি না তা জানার জন্য প্রকাশকের ইতিহাস যাচাই
করা একটি গুরুত্বপূর্ন প্রধান ধাপ। মর্যাদাপূর্ন প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারনত
সাংবাদিকতার মানদন্ড মেনে চলে এবং তাদের প্রকাশনায় ধারাবাহিকতা বজায় রাখে।
সুতরাং, আপনি যে উৎস থেকে খবর পড়ছেন তা সুপরিচিত কিনা এবং তাদের সঠিকভাবে
রিপোর্টিং করার রেকর্ড রয়েছে কিনা তা যাচাই করে দেখুন।
"আমাদের সম্পর্কে" পৃষ্ঠাটি দেখুনঃ প্রকৃত সংবাদপত্রগুলোর ওয়েবসাইটের "আমাদের সম্পর্কে" বা "About Us"
পেজে সাধারনত স্বচ্ছভাবে মালিকানার তথ্য, সম্পাদকীয় নীতিমালা, এবং ঐ প্রতিষ্ঠানে
স্থায়ীভাবে কাজ করা সিনিয়র সাংবাদিকদের তালিকা দেওয়া থাকে। এই তথ্যগুলো পাঠকদের ঐ
প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, মূল্যবোধ এবং জবাবদিহিতা সম্পর্কে ধারনা দেয়। যদি কোন
সংবাদ পত্রের ওয়েবসাইটে এসব তথ্যগুলো পরিস্কারভাবে না দেওয়া থাকে তবে সেই
ওয়েবসাইটের প্রকাশ করা সংবাদগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সতর্ক থাকা উচিৎ।
উত্তেজনাপূর্ন নামের ওয়েবসাইট সম্পর্কে সতর্ক থাকুনঃ বৈধ সংবাদ মাধ্যমের অনুকরনে তৈরি ডোমেইন বা অতিরঞ্জিত ভাষা ব্যাবহারকারী
নিউজ ওয়েবসাইটগুলো ফেক নিউজের অন্যতম প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করে। উত্তেজনাপূর্ন
নামগুলো ব্যাবহার করে অসৎ লোকেরা পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষন করতে চায় যাতে তারা আসল
তথ্য বিকৃত করে পাঠককে বিভ্রান্ত করতে পারে। উদাহরন স্বরূপ, ".com.co" দিয়ে শেষ
হওয়া ওয়েবসাইটগুলো নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানের অনুকরনে তৈরি হতে পারে; এগুলো
সাধারনত পাঠকদের বিভ্রান্ত করার জন্য বানানো হয়।
হেডলাইন চেক করুন
ফেক নিউজে প্রায়ই পাঠকদের মনযোগ আকর্ষন করার জন্য চাঞ্চল্যকর বা ক্লিকবেইট
শিরোনাম ব্যাবহার করা হয়। এই শিরোনামগুলো এমনভাবে লেখা হয় যাতে তা আমাদের কৌতুহল
জাগিয়ে তোলে এবং আমাদের আবেগকে প্রভাবিত করে আমাদেরকে ক্লিক করতে উৎসাহ দেয়।
সাধারনত এগুলো তথ্যের নির্ভুলতার চেয়ে চমকপ্রদ উপস্থাপনার উপর জোর দেয়, যার ফলে
এই ধরনের সংবাদকে সাবধানতার সাথে বিবেচনা করতে হবে। এই হেডলাইনগুলোতে
প্রায়ই দেখা যায়ঃ
অতিরঞ্জিতাঃ যেসব ওয়েবসাইট থেকে ফেক নিউজ
প্রকাশ করা হয় সেখানে অতিরঞ্জিত শব্দ ব্যাবহার করা একটি সাধারন কৌশল; তারা তাদের
শিরোনামে প্রায়ই "অবিশ্বাস্য", "ব্রেকিং", বা "আপনি বিশ্বাস করবেন না" এই জাতীয়
শব্দগুলো ব্যাবহার করে পাঠকদের উত্তেজিত করার চেষ্টা করে। একটা তুচ্ছ ঘটনাকে
বাড়িয়ে বাড়িয়ে তিলকে তাল বানানোর মাধ্যমে তারা পাঠকদের ঐ বিষয়টি নিয়ে ভালো ভাবে
চিন্তা ভাবনা করতে বাধা দিয়ে তাৎক্ষণিক সাড়া দিতে উস্কানি দেয়। অতিরঞ্জিত বা
বিভ্রান্তিকর দাবি উপস্থাপন করে, এই ধরনের শিরোনামগুলো পাঠকদের আর্টিকেল পড়ার
আগেই বিভ্রান্ত করে দেয়।
বড় হাতের অক্ষরের অতিরিক্ত ব্যাবহার (ইংলিশ আর্টিকেলে) ঃ অল ক্যাপস বা বড় হাতের অক্ষরের অতিরিক্ত ব্যাবহার আরেকটি সতর্ক সংকেত, যা
প্রায়ই পেশাদারিত্ব বা বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব নির্দেশ করে। ইনফর্মাল পরিবেশে
আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, এবং কলিগদের সাথে যোগাযোগের সময় জরুরী বার্তা বা কোন
কিছু নিয়ে হুজুগ বাড়ানোর জন্য অল ক্যাপস ব্যাবহার করা হয়। এটি সাধারনত
নির্ভরযোগ্য সাংবাদিকতায় দেখা যায় না, যেখানে সংযমী টোন এবং যথাযথ ফরম্যাটিং
ব্যাবহার করা হয়।
সাংঘাতিক ঘটনা দাবী করাঃ ফেক নিউজে
প্রায়ই সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেছে বলে দাবী করা হয়ে থাকে, তারা আপাত দৃষ্টিতে সাহসী
এবং অভাবনীয় শিরোনাম দিয়ে পাঠকদের মনযোগ আকর্ষন করতে চায়। এই ধরনের
শিরোনামগুলো সাধারনত তাদের দাবী সমর্থন করার জন্য কোন প্রমান দেয় না; এগুলো
পাঠকদের মনে চমক দেবার জন্য তৈরি করা হয়। পাঠকদের উচিৎ চরম ধারনা এবং প্রমানবিহীন
রিপোর্টিং সম্বলিত নিউজ আর্টিকেল সম্পর্কে সতর্ক থাকা।
আকর্ষনীয় শিরোনাম থাকলেই যে একটা নিউজ আর্টিকেল মিথ্যা হবে তা সবসময় সত্য নয়;
কিন্তু কোন নিউজ আর্টিকেল পাঠকদের মনে শক্তিশালী আবেগ জাগিয়ে তেমন কোন প্রাসঙ্গিক
বিষয়বস্তু প্রদান না করলে তার বিশ্বাসযোগ্যতার ব্যাপারে সন্দেহ হওয়া উচিৎ।
শিরোনামের বাহিরে গিয়ে পুরো আর্টিকেলটি সময় নিয়ে ভালোভাবে পড়ুন এবং মূল্যায়ন
করুন।
লেখকের সম্পর্কে জানুন
একটা সংবাদ প্রতিবেদন কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য তা ঐ প্রতিষ্ঠানে কাজ করা সাংবাদিকদের
দক্ষতা ও সুনামের উপর নির্ভর করে। ভুয়া সংবাদ প্রতিবেদনগুলো প্রায়ই অপরিচিত লেখক
বা এমন ব্যাক্তিদের দিয়ে লেখানো হয় যাদের বিষয়টি সম্পর্কে কোনো প্রমানিত দক্ষতা
নেই। লেখকের পরিচিত নিশ্চিত করতে হলেঃ
তাদের যোগ্যতা খুঁজুনঃ পেশাদার
সাংবাদিকদের সাধারনত তাদের কাজ প্রদর্শন করার জন্য প্রোফাইল বা পোর্টফোলিও থাকে।
এই প্রোফাইলগুলোতে প্রায়ই তাদের কাজ করার অভিজ্ঞতা, শিক্ষা গত যোগ্যতা, এবং
গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনার তথ্য উল্লেখ করা থাকে। এই যোগ্যতাগুলো যাচাই করতে পারলে
তারা যে বিষয় নিয়ে লিখে থাকে সে বিষয়ের উপর তাদের জানাশোনা ও কতটুকু দখল রয়েছে সে
সম্পর্কে ধারনা পাওয়া যায়।
সতর্ক সংকেতগুলোর দিকে নজর দিনঃ বেনামী
লেখক বা ছদ্মনাম নিয়ে চলা লেখকদের প্রায়ই সাংবাদিকতার মানদন্ড মেনে সঠিক সংবাদ
প্রকাশ করার কোন দায়বদ্ধতা থাকে না। লেখকদের পরিচয় যাচাই করা ছাড়া তাদের দক্ষতা
বা কি উদ্দেশ্যে তারা লিখছে তা মূল্যায়ন করা কঠিন হয়ে যায়। এভাবে অজ্ঞাতনামা হয়ে
লেখা প্রায়ই ভুল তথ্য ছড়ানোর একটি কৌশল হিসেবে কাজ করে।
আগেকার নিবন্ধগুলো যাচাই করুনঃ আপনার কাছে যদি কোন সাংবাদিক বা লেখকের প্রকাশিত তথ্যগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতা
নিয়ে সন্দেহ হয়, তাহলে আপনি তারা নিয়মিতভাবে নির্ভরযোগ্য বিষয়বস্তু প্রকাশ করে কি
না তা যাচাই করে দেখতে পারেন। তাদের আগের কাজগুলো পর্যালোচনা করলে নির্ভুলতা অথবা
পক্ষপাতিত্বের ধরনগুলো প্রকাশ পাওয়া যায়। ধারাবাহিকভাবে বিশ্বাসযোগ্য প্রতিবেদনের
ইতিহাস তাদেরকে সৎ এবং দক্ষ সাংবাদিক হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়; আবার নিয়মিত ভুল
এবং চাঞ্চল্যকর লেখা প্রকাশ করা তাদের এড়িয়ে চলতে শেখায়।
সংবাদ প্রকাশের তারিখ দেখুন
অর্থনৈতিক সংকট বা রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়ে ধুরন্ধর এবং অসৎ প্রকৃতির লোকেরা
পুরনো সংবাদ প্রতিবেদন সামাজিক মাধ্যমগুলোতে পুনরায় পোষ্ট করে বর্তমান ঘটনাকে ভুল
ভাবে ব্যাখ্যা করে রাষ্ট্র ও সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করে থাকে। একটি
সংবাদ প্রতিবেদন কখন প্রকাশ করা হয়েছে তা জানা থাকলে আপনি বর্তমান সময়ে তার
প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে সঠিক ধারনা পাবেন। এর জন্য আপনিঃ
প্রকাশনার তারিখ যাচাই করুনঃ আপনি কোন
নিউজ ওয়েবসাইট বা সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করা সংবাদ পড়ার সময় নিশ্চিত হয়ে নিন যে
প্রতিবেদনটি বর্তমান সময়ে চলমান ঘটনাগুলোর সাথে প্রাসঙ্গিক অবস্থায় আছে। পুরনো
নিবন্ধ সংকট বা ঝামেলার সময় পুনরায় প্রকাশ পেতে পারে। সবসময় প্রকাশনার তারিখ
যাচাই করা জরুরি যাতে পুরনো তথ্যকে সাম্প্রতিক সংবাদ বলে ভুল না করা হয়।
আপডেট খুঁজুনঃ কিছু সংবাদ প্রতিবেদনকে
মাঝে মাঝে নতুন তথ্য দিয়ে আপডেট করা হয়। এক্ষেত্রে আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যে
আপডেট করা সংবাদ প্রতিবেদন পরিবর্তিত পরিবেশকে প্রতিফলন করছে কিনা অথবা এটিকে
প্রকাশনার পর থেকে আদৌ আপডেট করা হয়েছে কিনা। কোন একটি বিষয়ের উপর সাম্প্রতিক সময়
পর্যন্ত ঘটে যাওয়া খবরের হালনাগাদ জানা থাকলে আপনি ঐ খবরটিকে ভালোভাবে বোঝার
ক্ষমতা অর্জন করবেন।
পুনর্ব্যবহৃত বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুনঃ কোন একটি বিষয় বা ঘটনা ভাইরাল হয়ে গেলে যখন সবাই ঐ বিষয় নিয়ে প্রতিবেদন
তৈরিতে ব্যাস্ত হয় পড়ে, তখন সামাজিক মাধ্যমে একই ধরনের বিষয় নিয়ে করা পুরাতন
সংবাদ ছড়িয়ে দিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়। এসব পুরোনো খবরকে নতুন বলে
চালিয়ে দিয়ে অসৎ ব্যাক্তিরা তাদের নিজেদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে পাঠকদের মনকে
প্রভাবিত করতে চেষ্টা করে। বিভিন্ন সুত্র থেকে তথ্য যাচাই করা নতুন খবর
এবং পুনর্ব্যবহৃত বিষয়বস্তুর মধ্যে পার্থক্য করতে সাহায্য করে।
প্রতিবেদনের বিষয় চেক করুন
ফেক নিউজ বা ভুয়া সংবাদ প্রতিবেদনে প্রায়ই সহজেই চিহ্নিত করা যায় এমন ভুল থাকে,
এবং কোন একটি নির্দিষ্ট এজেন্ডার প্রতি তাদের লক্ষণীয় পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়।
এছাড়াও ফেক নিউজ আর্টিকেলে ছবি বা ভিডিও বিকৃত করে প্রকাশ করার প্রবণতা দেখা যায়।
ভিজ্যুয়াল কনটেন্টগুলোর সত্যতা যাচাই করতে আপনি গুগলের রিভার্স ইমেজ সার্চের মত
টুলগুলো ব্যাবহার করতে পারেন।
ব্যাকরণগত ভুল শনাক্ত করুনঃ নামকরা এবং
বৈধ সংবাদপত্রগুলো সাধারনত উচ্চ মানের সম্পাদকীয় নীতিমালা মেনে চলে। কোন অনলাইন
নিউজ ওয়েবসাইট নিয়মিত ব্যাকরণগত ভুল, বানানের ভুল এবং ভুলভাবে গঠিত বাক্য দিয়ে
লেখা আর্টিকেলগুলো প্রকাশ করলে তা সেখানে কাজ করা লোকদের পেশাদারিত্বের অভাব
সম্পর্কে পাঠকদের নেতিবাচক ধারনা দেয়। এই ধরনের ভুলগুলো থেকে ধারনা পাওয়া যায় যে
প্রতিবেদনটি দ্রুত এবং সঠিকভাবে পর্যালোচনা ছাড়া তৈরি করা হয়েছে, যা ফেক নিউজের
অন্যতম প্রধান একটি লক্ষন।
অতিরিক্ত পক্ষপাত খুজুনঃ যেসব আর্টিকেল,
বিশেষ করে যেসব আর্টিকেল রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে লেখা হয়ে থাকে, তারা যদি একটি
দৃষ্টিভঙ্গিকে অতিরিক্ত সমর্থন করে এবং বিপরীত মতামতকে ইচ্ছা করে উপেক্ষা করে
থাকে, সেসব আর্টিকেলগুলো সন্দেহের সাথে পড়া উচিৎ। একটি ভারসাম্যপূর্ণ সংবাদ
প্রতিবেদন পাঠকদের কোন একটি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত জানানোর জন্য ঐ বিষয়টির উপর
বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিকে অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। অতিরিক্ত পক্ষপাতযুক্ত প্রতিবেদন
পাঠকদের আবেগ নিয়ে খেলা করার জন্য লিখা হতে পারে অথবা তাদেরকে উস্কানি দেওয়ার
জন্যও প্রকাশ করা হতে পারে।
প্রতিবেদনের মধ্যে উল্লিখিত সূত্রগুলো যাচাই করুনঃ নির্ভরযোগ্য নিউজ ওয়েবসাইটগুলো তাদের প্রকাশ করা প্রতিবেদনগুলোতে তাদের
দাবির সমর্থনে বিশ্বস্ত তথ্য এবং বিশেষজ্ঞদের মতামত উল্লেখ করে। এই সূত্রগুলো
বিশ্বাসযোগ্য এবং প্রতিবেদনের বিষয়ের সাথে প্রাসঙ্গিক কিনা তা যাচাই করে দেখুন।
যথাযথ সুত্রের অভাব এবং অস্পষ্ট তথ্যের উপর নির্ভরতা ফেক নিউজ চেনার একটি অন্যতম
সতর্ক সংকেত হতে পারে।
প্রতিবেদনের তথ্যগুলোকে ক্রস রেফারেন্স করুন
ফেক নিউজ সনাক্ত করার একটি অন্যতম কার্যকর পদ্ধতি হলো এটিকে অন্যান্য উৎস থেকে
পাওয়া প্রতিবেদনের সাথে তুলনা করা। এভাবে তথ্য যাচাই করা শুধু একটি প্রতিবেদনের
সত্যতা নিশ্চিত করে না, বরং প্রতিবেদনের বিষয়টিকে আরও ভালোভাবে জানতে আমাদের
সাহায্য করে। কোন সংবাদ প্রতিবেদনকে সন্দেহজনক মনে হলে আপনিঃ
খবরের সত্যতা নিশ্চিত করতে অন্যান্য সুত্র খুঁজুনঃ আপনি চেক করে দেখুন অন্যান্য নামকরা নিউজ ওয়েবসাইটগুলো একই খবর
রিপোর্ট করছে কিনা। নির্ভরযোগ্য সংবাদ প্রায়ই একাধিক বিশ্বস্ত নিউজ ওয়েবসাইটে
প্রকাশিত হয়ে থাকে। আবার, প্রতিবেদনটি যদি শুধু কোন একটি অখ্যাত ও অপরিচিত সাইটে
প্রকাশ পেয়ে থাকে, তাহলে সেটির ভুয়া সংবাদ হবার সম্ভাবনা বেশি হয়ে থাকে।
ধারাবাহিকতার দিকে খেয়াল রাখুনঃ কোন
সংবাদ প্রতিবেদনে গুরুত্বপুর্ন তথ্যগুলো উল্লেখ করা না থাকলে অথবা মূল তথ্যগুলোর
মধ্যে অসামঞ্জস্যতা দেখা দিলে ঐ প্রতিবেদনটির ফেক নিউজ হবার ইঙ্গিত দেয়। এসব
অসামঞ্জস্যতা সনাক্ত করার জন্য একই সংবাদকে ভিন্ন ভিন্ন উৎস থেকে কেমন করে
রিপোর্টিং করা হয়েছে তার তুলনা করুন। একাধিক উৎস থেকে প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনে
তথ্যের ধারাবাহিকতার মিল পাওয়া তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ায়।
ফ্যাক্ট-চেকিং ওয়েবসাইটের উপর নির্ভর করুন (আন্তর্জাতিক খবরের ক্ষেত্রে)
ঃ Snopes, FactCheck.org, এবং PolitFact এর মতো প্লাটফর্মগুলো খবরের সত্যতা
যাচাইয়ের জন্য ভালো মাধ্যম হতে পারে। এই ওয়েবসাইটগুলো সন্দেহজনক খবরের ব্যাপারে
ব্যাপক বিশ্লেষন এবং তার প্রেক্ষাপট প্রদান করে। এগুলোর মাধ্যমে আপনি একটা সংবাদ
প্রতিবেদনের সত্যতা যাচাই করতে পারবেন।
প্রতিবেদনের টোন এবং উদ্দেশ্য নির্নয় করুন
একটি সংবাদ প্রতিবেদনের টোন এর সত্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে অনেক কিছুই
প্রকাশ করতে পারে। ফেক নিউজ বা ভুয়া সংবাদ প্রায়ই পাঠকদের উত্তেজিত করে রাগিয়ে
দিতে, ভয় দেখাতে, এবং কোন একটা বিষয় নিয়ে অযথা তর্ক সৃষ্টি করতে নানা রকম কৌশলের
আশ্রয় নিয়ে থাকে। একটি সংবাদ প্রতিবেদনের পেছনের উদ্দেশ্য বুঝতে পারা পাঠকদের বৈধ
সাংবাদিকতা এবং ইচ্ছা করে ভুল তথ্য দিয়ে তৈরি করা ফেক নিউজের মধ্যে পার্থক্য করতে
সহায়তা করে।
আবেগপ্রবন আবেদনঃ যেসব সংবাদ প্রতিবেদনে
রাগ, ভয় বা ক্ষোভ উস্কে দিতে তৈরি করা হয়, সেগুলোতে প্রায়ই তথ্যের নির্ভুলতার
চেয়ে চাঞ্চল্যকর উপস্থাপনার উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই ধরনের প্রতিবেদনগুলোতে
সাধারণত আবেগপ্রবন ভাষা ব্যাবহার করে পাঠকদের মাঝে শক্তিশালী নেতিবাচক
প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা হয়। এভাবে তারা পাঠকদের আবেগ নিয়ে খেলা করার মাধ্যমে
পাঠকদের প্রতিবেদনের বিষয়বস্তুগুলো ভালো করে যাচাই করার প্রয়োজনীয়তা থেকে মনযোগ
সরিয়ে দেয়।
প্রোপাগান্ডাঃ যেসব নিবন্ধ নির্দিষ্ট
উদ্দেশ্য বা মতাদর্শ প্রচার করার জন্য লেখা হয়ে থাকে, সেগুলোতে প্রায়ই ইচ্ছে করে
তথ্যের সঠিক হবার ব্যাপারে কম মনযোগ দেওয়া হয়। এসব নিবন্ধের লেখকেরা তাদের
রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় এবং অর্থনৈতিক মতবাদ সমর্থন করার জন্য বাছাইকৃত এবং
একপাক্ষিক তথ্য উপস্থাপন করে এবং তাদের মতবাদকে সমর্থন করে না এমন প্রমাণগুলোকে
এড়িয়ে যায়। এই জাতীয় নিবন্ধগুলোর লেখকদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বোঝার জন্য এই ধরনের
পক্ষপাতিত্ব চিহ্নিত করা দরকার।
সংবাদ প্রতিবেদনের সাথে পাঠকদের অংশগ্রহন খেয়াল করুন
একটি সংবাদ প্রতিবেদনকে পাঠকেরা কেমন করে গ্রহন করে, ঐ বিষয়ে তাদের মতামত কি এসব
জিনিস যাচাই করে ঐ সংবাদ প্রতিবেদনের নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে আরও তথ্য পাওয়া যায়।
যদিও শুধু পাঠকদের কমেন্ট দিয়েই একটি নিবন্ধের সত্যতা যাচাই করা উচিৎ নয়, তারপরেও
তারা ঐ নিবন্ধের সম্ভাব্য সমস্যাগুলো ব্যাপারে পাঠকদের সর্তক করতে পারে। যেসব
বিষয়গুলো আপনাকে বিবেচনায় রাখতে হবেঃ
মন্তব্য বিশ্লেষণ করুনঃ কোন একটি অনলাইন
নিউজ ওয়েবসাইটে প্রকাশিত কোন একটি সংবাদ প্রতিবেদনের কমেন্ট বক্সে পাঠকরা ঐ
প্রতিবেদনের তথ্যগত ভুল এবং অসামঞ্জস্যতা প্রমানসহ ধরিয়ে দিলে, ঐ নিবন্ধের ফেক
নিউজ হবার ভালো সম্ভাবনা রয়েছে। অনলাইন নিউজ ওয়েবসাইটে মন্তব্য করার জায়গাগুলো
প্রায়ই পাঠকদের ঐ ওয়েবসাইটে প্রকাশিত খবরগুলোকে প্রশ্ন করা বা সমালোচনা করার একটি
স্থান হিসেবে কাজ করে। এই প্রতিক্রিয়াগুলো পর্যালোচনা করলে সংবাদ প্রতিবেদনের
বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে মুল্যবান তথ্য পাওয়া যায়।
পাঠকদের মূল্যায়ন করুনঃ একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে টার্গেট করে লেখা আর্টিকেল পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে
থাকে। এই ধরনের নিবন্ধ প্রায়ই তথ্য বিকৃত করে একটি নির্দিষ্ট বিশ্বাস বা আবেগকে
আকৃষ্ট করার জন্য লেখা হয়ে থাকে। কাদের কথা মাথায় রেখে আর্টিকেলটি লেখা হয়েছে তা
জানা থাকলে আর্টিকেলটি কোন উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে সে ব্যাপারে একটি ভালো ধারনা
পাওয়া যায়।
বট চিহ্নিত করুনঃ একই ধরনের কমেন্ট
বারবার পোষ্ট করে স্বয়ংক্রিয় অ্যাকাউন্টগুলো ফেক নিউজ প্রচারে সাহায্য করে।
এধরনের স্বয়ংক্রিয় অ্যাকাউন্ট বা বটগুলো প্রতিবেদনের বিষয়বস্তুগুলো বাস্তবে যত না
জনপ্রিয়, তাকে তার চাইতে অনেক বেশি জনপ্রিয় বা বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার চেষ্টা
করে। এমন আচরন চিহ্নিত করতে পারার ক্ষমতা আপনাকে উদ্দেশ্যমুলক ভাবে সাজানো এবং
বিকৃত তথ্যে ভরা সংবাদ প্রতিবেদন চিনতে সাহায্য করবে।
তথ্যগুলোর সত্যতা যাচাইয়ে বিশেষ সাহায্য নিন
আপনি যদি জটিল বা প্রযুক্তিগত নিবন্ধের সঠিকতা যাচাই করতে চান তাহলে ঐ বিষয়ের
বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া একটি মুল্যবান কৌশল হতে পারে। এই কাজের জন্য একাডেমিক
জার্নাল, ফ্যাক্ট চেকিং ওয়েবসাইট, এবং খ্যাতনামা থিঙ্ক ট্যাঙ্কের মতো
প্লাটফর্মগুলো বিশেষজ্ঞ মতামতের একটি চমৎকার উৎস হতে পারে। বিশেষজ্ঞ মতঃ
প্রেক্ষাপট প্রদান করেঃ বিশেষজ্ঞদের
মতামত পাঠকদের জটিল বিষয়গুলো বিভিন্ন দিক থেকে চিন্তা করিয়ে নিয়ে করে একটা
সম্পুর্ন প্রেক্ষাপট প্রদান করে। এসব প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলো পাঠকদের প্রতিবেদনটি
আরও গভীরভাবে মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে। এর অভাবে, জটিল বিষয়গুলো অতিসরলীকৃত বা
ভুলভাবে উপস্থাপিত হয়ে পাঠকদের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।
ভুল তথ্য খণ্ডন করেঃ বিশেষজ্ঞদের মতামত
পাঠকদের ভুয়া দাবিগুলোকে চিহ্নিত করতে এবং সেগুলো সংশোধন করতে শিখায় যাতে সেগুলো
ছড়িয়ে না পড়ে। ফেক নিউজ মোকাবেলার জন্য তথ্য বাছাই এবং পাঠকদের সামনে সংবাদ
প্রতিবেদনে উল্লেখ করা তথ্যের সততার প্রমান উপস্থাপন করা অত্যন্ত জরুরি। এই
প্রক্রিয়াটি শুধু ভুল তথ্যকে বাদ দেয় না, বরং পাঠকদের কিভাবে ভুলগুলো চিহ্নিত
করতে হয় তাও শেখায়।
বোধগম্যতা বাড়ায়ঃ পাঠকদের বিভ্রান্ত করতে
ফেক নিউজে প্রায়ই কঠিন শব্দ ও টেকনিক্যাল ভাষা ব্যাবহার করা হয়; সেক্ষেত্রে ঐ
বিষয় নিয়ে কাজ করা বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে এরকম প্রযুক্তিগত ভাষা পাঠকদের কাছে
স্পষ্ট করা যায়। জটিল ভাষার সরলীকরণ নিবন্ধের তথ্যগুলোকে পাঠকদের কাছে আরও
সহজলভ্য এবং স্বচ্ছ করে তোলে। এভাবে লেখক ও পাঠকদের মাঝে পরিস্কার যোগাযোগ
পাঠকদের নিবন্ধ সম্পর্কে সঠিক ধারনা তৈরি করতে সাহায্য করে।
শেষ কথা
তথ্যের জোয়ারে ভেসে যাওয়া এই বিশ্বে ফেক নিউজ চিনতে পারার দক্ষতা ইন্টারনেট
ব্যাবহারকারীদের জন্য প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। ভুল ও ক্ষতিকর তথ্য থেকে রক্ষা পেতে
পাঠকরা সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা প্রয়োগ এবং নির্ভরযোগ্য টুলস্ ব্যাবহার করে
বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ এবং বিভ্রান্তিকর তথ্যের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে।
সবশেষে বলা যায়, গনমাধ্যম নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি শুধু পাঠকদের সঠিক সিদ্ধান্ত নিতেই
সহায়তা করে না, বরং এটি স্বাস্থ্যকর মিডিয়া পরিবেশ তৈরি করতেও অবদান রাখে। আমরা
সবাই মিলে তথ্যের সঠিকতা নিশ্চিত করে, সংবাদপত্রের জবাবদিহিতা এবং সত্যের প্রতি
আমাদের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করে ফেক নিউজের বিস্তার রোধ করতে পারি।


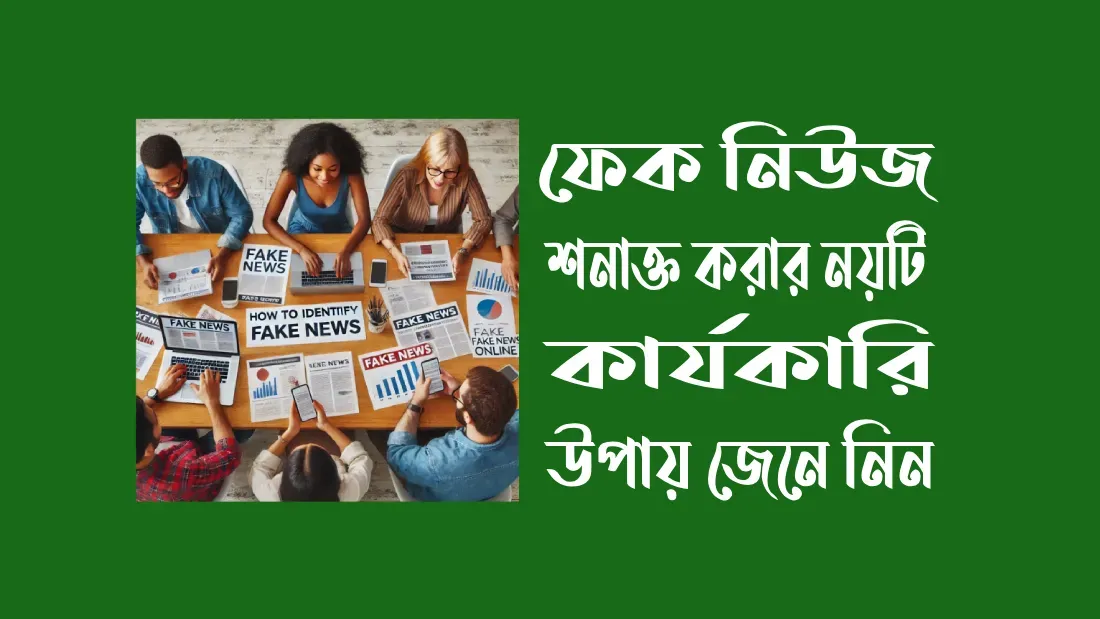






আমার ব্লগের নীতিমালা মেনে কমেন্ট করুন। প্রতিটি কমেন্ট রিভিউ করা হয়।
comment url